মুকুল কান্তি ত্রিপুরা[1]
যে সকল ধ্বনি সমষ্টির দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে কক বা ভাষা বলা হয়। আর ত্রিপুরা বা বরক জাতির মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তাকেই ‘ককবরক ভাষা’ বলা হয়ে থাকে। এই ‘ককবরক’ (Kokborok) শব্দটি মূলত একটি যৌগিক শব্দ। একটি শব্দ ‘কক’ এবং অপরটি ‘বরক’, এ দু’টি শব্দ মিলে এ ককবরক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আর শাব্দিক অর্থে ‘কক্’ এর বাংলা অর্থ ‘ভাষা’ আর ‘বরক’ এর বাংলা অর্থ ‘মানুষ’। এখানে মানুষ বলতে ত্রিপুরাদেরকেই বুঝানো হয়েছে।
ফরাসী ভাষাবিদ Dr. Francois Jacquesson তাঁর ‘KOK-BOROK, A SHORT ANALYSIS’ নামক গ্রন্থে ককবরক এর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন-
“Kokborok, the language of the Borok people, belongs to the large Tibeto-Burmese group. This group of about 250 languages, spoken in Eastern Asia, is related to the Chinese languages with which it forms the Sino-Tibetan super-group.”
ককবরক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হল খুগনি কক বা কথ্য ভাষা এবং অপরটি হল সুইজাক কক বা লিখিত ভাষা। অর্থাৎ মনের ভাব মুখে বলে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হয় খুগনি কক বা কথ্য ভাষা। অপরদিকে মনের যে ভাব লিখে প্রকাশ করা হয় তাকে সুইজাক কক বা লিখিত ভাষা বলা হয়।
ককবরক ভাষার উৎপত্তি:
পৃথিবীর যে কোন ভাষার রয়েছে একটি উৎপত্তির ইতিহাস। যা নির্ধারিত হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাষা পরিবারের অন্তর্ভূক্তির মধ্য দিয়ে। ভাষাবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল ভাষাকে কয়েকটি ভাষা পরিবারে বিভক্ত করে ঐ ভাষাপরিবারের মধ্যে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আবিস্কার করেছেন বিভিন্ন ভাষার উৎস। যেমন: ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতী , অস্ট্রেলীয়, আফ্রো-এশীয়, অস্ট্রো-এশীয়, অস্ট্রোনেশীয়, নাইজার-কঙ্গো, আন্তঃ-নিউ গিনি, নীল-শাহারা, দ্রাবিড় ইত্যাদি। তেমনি ককবরক ভাষাও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে একটি ভাষা পরিবারে এবং তাকেই এ ভাষার উৎপত্তির মূল সূত্র বলে ধরে নেওয়া হয়। ভাষাবিদরা এই ভাষাকে চীনা-তিব্বতীয়(Sino-Tibetan) বিভাগের ভোট-বমী (Tibeto-Barmese) গোত্রের ‘Bodo’ দলের অন্তর্ভূক্ত একটি ভাষা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাহলে ককবরক ভাষা চীনা-তিব্বতী( ঝরহড়-ঞরনবঃধহ) ভাষা থেকে কিভাবে উৎপত্তি হল তা নি¤েœ ছক আকারে প্রদত্ত হল:
SINO-TIBETAN
Chinese Thai Tibeto-Burmise
Boro Burmise Tibetan
Chutia Dimasa Garo Hojai Kokborok Kuch Mech Rabha Tiwa(Lalung)
উপরোক্ত ছকে প্রদত্ত ভাষাগোষ্ঠীগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, পন্ডিতগণ ককবরক ভাষাকে চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবারে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এই চীনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারকে প্রথমে তিনটি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয় । যেমন- চীনা , থাই এবং ভোট-বর্মী। এই ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- বোরো, বমী এবং তিব্বতী। আবার এই বোরো ভাষাগোত্র থেকে উৎপত্তি হয়েছে চুটিয়া, দিমাছা, গারো, হজাই, ককবরক, কোচ, মেচ, রাভা এবং তিওয়া ভাষাগুলো।
এখানে দেখা যাচ্ছে, চীনা ভাষা, তিব্বতী ভাষা, বর্মী ভাষা এবং বোরো ভাষার সাথে ককবরক ভাষার একটি দারুন যোগসূত্র রয়েছে। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় । তাহলে চীনা ভাষা সম্পর্কেও একটু পরিচয় দিই। চীনা-তিব্বতীয় ভাষাপরিবারের চীনা শাখার ভাষাসমূহ অনেক সময় চীনা ভাষা নামে পরিচিত। যদিও ম্যান্ডারিন চীনা ভাষাটি গণচীন ও চীন প্রজাতন্ত্রের (তাইওয়ান) একমাত্র সরকারি ভাষা। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, চীনা ভাষাগোষ্ঠীতে সাত কিংবা দশটি ভাষা বা উপভাষাগোষ্ঠী আছে। হান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ এবং অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ভাষায় কথা বলে। বিশ্বের প্রায় ১২০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা চীনা। আর তিব্বতি ভাষা তিব্বতি-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম একটি ভাষা, যা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরে, মধ্য এশিয়ার পূর্বভাগে তিব্বতি জাতির লোকদের বিভিন্ন মুখের ভাষার সাধারণ নাম। এগুলিও নিসন্দেহে চীনা-তিব্বতি ভাষাপরিবারের সদস্য। এ ভাষা মধ্য এশিয়ার মধ্যে বাল্টিস্তান, তিব্বতী মালভূমি ও হিমালয় সহ ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তিব্বতী, লাদাখ, নেপাল, সিকিম, ভুটান ও অরুনাচল প্রদেশে কথিত। পৃথিবীতে ৬০ লক্ষেরও বেশি তিব্বতি ভাষাভাষী মানুষ আছেন। এবার আলোচনা করা যাক বর্মী ভাষা কী? বর্মী ভাষা বা মায়ানমার ভাষা চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবারের তিব্বতী-বর্মী শাখার একটি ভাষা। বর্তমানের মায়ানমারের অধিকাংশ জনগণ এই বর্মী ভাষার কোন না কোন আঞ্চলিক উপভাষায় কথা বলেন। বর্মী ভাষার প্রথমে পালি ও পরে মোন ভাষার (১২শ -১৩শ শতক) প্রভাব পড়ে। এরপর ১৬শ থেকে ১৯শ শতক পর্যন্ত ভাষাটি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা যেমন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার সংস্পর্শে আসে। এই ভাষাগুলি কথ্য বর্মী ভাষাকে প্রচুর প্রভাবিত করে, তবে এগুলি লিখিত বর্মী ভাষায় তেমন কোন পরিবর্তন আনেনি। বর্তমানে বর্মী ভাষা মায়ানমারের রাষ্ট্রভাষা।
এবার আলোচনায় আসি ককবরকের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি নিয়ে, চীনের উত্তর পশ্চিমে ইয়াংসি এবং হোয়ংহু নদীর উৎসস্থলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ককবরক ভাষার জন্ম বলে ধারণা করা হয়। মূলত এশিয়া থেকে দক্ষিণে বার্মা এবং বালিষ্টান থেকে পেকিং পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলজুড়ে মানুষজন যে ভাষায় কথা বলে তাকে টিবেটো চাইনিজ বলা হয়ে থাকে। এই তিবেটো চাইনিজ বা সিনো টিবেটান ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি হলো শ্যামীজ-চাইনিজ(থাই-চীনা) এবং অপরটি হল তিবেটো বর্মণ। এই তিবেটো বর্মণ ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম একটি ভাষা হচ্ছে ‘বডো’ বা ‘বরো’। আর এই বডো বা বরো থেকেই কক্বরক ভাষার উৎপত্তি। গারো, বোড়ো, কাছারী, দিমাসা, রাভা, মেচ, কোচ, ত্রিপুরা প্রভৃতি এ দলের অন্তর্ভূক্ত ভাষা।
বর্তমানে এই ভাষার অধিকাংশ প্রচলন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকলেও বার্মা, নেপাল, ভূটান এবং বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায়ও এর প্রচলন রয়েছে।
ককবরক ভাষার লিখিরেূপে নামকরণের ইতিহাস:
‘ককবরক’ ভাষার কথ্য ও লিখিত ব্যবহার অতি প্রচীন হলেও ‘ককবরক’ নামের নামকরণ ও শব্দটির ব্যবহার ঊনবিংশ শতকের শেষ অথবা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বলে অনেক গবেষক মনে করেন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরাদের ভাষার নাম হিসেবে ককবরক নামকরণটি বোধহয় খুব বেশি প্রচলন ছিল না। কেননা ককবরক ভাষাটি ত্রিপুরাদের নিকট কখনো কখনো তিপারাকক্, তিপ্রাকক্ বা ত্রিপুরাকক্ নামেও পরিচিত ছিল। কখনো কখনো আবার ত্রিপুরী ভাষাও বলা হয়ে থাকে। এই নামগুলো তিপ্রা, তিপারা বা ত্রিপুরা জাতির নামানুসারেই হয়তোবা প্রচলিত হয়েছিল ক্ষুদ্র আঙ্গিকে। যেমনটি দিমাছাদের ভাষার নাম দিমাছা, গারোদের ভাষার নাম গারো, অহমিয়াদের ভাষার নাম আসামী, কোচদের ভাষ নাম কোচ, রাভাদের ভাষার নাম রাভা, চাকমাদের ভাষার নাম চাকমা ইত্যাদি হয়েছিল। অর্থাৎ নিজ নিজ জাতির নামানুসারে ভাষার নামগুলোর নামাকরণ করা হয়েছে। তাই ইতিপূর্বে ককবরক ভাষাকে কি কি নামে অভিহিত করা হয়েছে সেগুলো নি¤েœ ব্যখ্যা প্রদান করা হলো:
শ্রী রাজমালার দ্বিতীয় লহরের ব্যাখ্যা:
কথিত আছে, প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য ককবরক ভাষায় কলমা বা কোলোমা লিপিতে দুর্লবেন্দ্র চোনতাই লিপিবদ্ধ করেছিলেন ‘রাজরতœাকর’ নামক একটি গ্রন্থ। পরবর্তীতে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর নামের দুই ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করে এবং পরবর্তীতে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পূর্বের রাজমালা যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ ‘শ্রী রাজমালা’র দ্বিতীয় লহরের ধর্ম মাণিক্য খন্ডের ৬ নং পৃষ্ঠায় নি¤œরূপ স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে-
“পূর্ব রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে।
পয়ার গাথিল সব সকলে বুঝিতে॥
সুভাষাতে ধর্ম্মরাজে রাজমালা কৈল।
রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল ।।”
অর্থাৎ শ্রী রাজমালায়ও ‘ককবরক’ ভাষা নামে কোন শব্দের সন্ধান মেলেনি। সেখানেও ‘ত্রিপুর ভাষা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । পূর্বে ‘ককবরক’ শব্দটি ত্রিপুরাদের ভাষার নাম হিসেবে ব্যবহৃত ছিল না বরং ভাষাবিদগণও বিভিন্ন নামে এই ভাষার নামকরণ করেছেন।
ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমার চট্ট্যোপাধ্যায় তাঁর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language) গ্রন্থের Introducton এর ৩ নং পৃষ্ঠায় ত্রিপুরাদের ভাষা হিসেবে Mrung অথবা Tipura শব্দগুলোকে ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন-
“To the north-east and east, Bengali meet dialects of the Bodo group: Bodo (Bara) of Kachari (also known as koc, Mec and Rabha), Garo and Dima-sa as well as Mrung or Tipura.”
অর্থাৎ তিনিও ককবরক ভাষার নামকরণে ককবরক (Kokborok) শব্দটি ব্যবহার করেন নি।
অন্যদিকে Sir George Abraham Grierson সাহেবও তার সম্পাদিত ১৯০৯ সালে প্রকাশিত Linguistic Survey of India (Vol.111, Part.11) গ্রন্থের ১০৯ নং পৃষ্ঠায় ত্রিপুরাদের ভাষার নাম Tipura উল্লেখ করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাদের ভাষা হিসেবে নামকরণ করেছেন Mrung । তিনি লিখেছেন-
‘In the Chittagoong Hill Tracts the language is also called Mrung ’
আবার তিনি ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ব্যবহার করতে গিয়ে উক্ত গ্রন্থে Tipura নামটিও ব্যবহার করেছেন ।
তবে বর্তমানে Mrung শব্দটি মারমা ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত রয়েছে। তারা ত্রিপুরাদেরকে Mrung বলে থাকে।
অর্থাৎ গ্রিয়ার্সন সাহেবও এ ভাষার নাম হিসেবে Mrung শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
সুনীতি কুমার ও গ্রিয়ার্সন ককবরক ভাষার নামকরণে Mrung শব্দটি ব্যবহার করলেও উইলিয়াম হান্টার তাঁর A Statistical Account of Bengal গ্রন্থে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ত্রিপুরাদের ভাষার নামের পরিবর্তে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীকে Mrung নামে অভিহিত করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন-
“The whole of the tipperah tribe is known to the Khyoungtha of the Chittagong Hill Tracts by the name of Mrung. And the Arakanese apply the same name to the descendants of Tipperahs found in the Akyab District.”
দেখা যাচ্ছে, শ্রী কালীপ্রসন্নসেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত ‘শ্রীরাজমালা’, ভাষাচার্য Suniti Kumar Chatterji এর ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language), স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন এর ‘Lunguistic Survey of India’ এবং উইলিয়াম হান্টার এর A Statistical Account of Bengal গ্রন্থগুলোতে কোথাও ‘ককবরক’ (Kokborok) শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনামলে ত্রিপুরার ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট সি. ডাব্লিউ বোল্টন এর রিপোর্ট(১৮৭৬-৭৭) থেকে জানা যায় যে, যুবরাজ রাধাকিশোর একটি তিপারা-বাঙলা অভিধান সংকলনের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। বোল্টন সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন,
“The Jubraj is Still engaged in the compilation of a Tipperah- Bengali dictionary. And he has lately become a member of the Asiatic Society of Bengal”
তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগার কথা, এই ত্রিপুরাদের ভাষার বর্তমান নাম ‘ককবরক’ শব্দটি কিভাবে উৎপত্তি হলো? কেইবা প্রথম ব্যবহার করলো এই শব্দটি?
এই প্রশ্নে উত্তর খুঁজে পাওয়া বর্তমানে আর কোন কঠিন কাজ নয়। কেননা ত্রিপুরাদেরই একজন এক্ষেত্রে পথিকৃত ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর তিনি হলেন সেনাপতি শ্রী রাধামোহন ঠাকুর । তিনি একাধারে ছিলেন বিচারপতি, সেনাপতি, লেখক ও গবেষক। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রচিত ‘কক্-বরক্-মা’(ত্রৈপুর ভাষার ব্যাকরণ) নামক গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ‘ককবরক’ এর সূত্রপাত করেন। এ গ্রন্থটি শ্রী একাজদ্দিন আহমদ ১৩১০ ত্রিপুরাব্দে চৈতন্য যন্ত্র- কুমিল্লা থেকে প্রকাশ করেন। মূলত তাঁর ‘কক্-বরক্-মা’(ত্রৈপুর ভাষার ব্যাকরণ) গ্রন্থ রচনা থেকেই প্রথম ‘ককবরক’ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ‘কক্’ এর বাংলা অর্থ ‘ভাষা’ আর ‘বরক’ এর বাংলা অর্থ ‘মানুষ’ অর্থাৎ মানুষের ভাষা এই অভিধায় নামাঙ্কিত করেছেন তিনি। এর পিছনে কাছ করেছে একটি মহান মানবতা এক অপূর্ব কাব্যিক ভাবনা। ইতিপূর্বে হয়তোবা ত্রিপুরাদের ভাষার নাম হিসেবে খুব বেশি প্রচলিত ছিল ‘ত্রিপুরী ভাষা’ বা ‘ত্রিপুরা ভাষা‘। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যে গ্রন্থের নাম যেমন রেখেছিলেন ‘কক্-বরক্-মা’ তেমনি গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছিলেন “যে শাস্ত্র দ্বারা কক্-বরক (ত্রিপুরী ভাষা) শুদ্ধরূপে লেখা এবং বলা হয় তাহার নাম কক্-বরক্-মা (ত্রিপুরী ব্যাকরণ)।” এছাড়াও তিনি ককবরক ভাষায় আরও দু’টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি হলো ‘ত্রৈপুর ভাষাভিধান’(১৯০৭) এবং অপরটি হলো ‘ত্রৈপুর কথামালা’(১৯০৯) ।
ভাষাবিদ কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী তাঁর ‘ককবরক ভাষার পরিচয়’ প্রবন্ধে লিখেছেন-
“ ককবরক ভাষার নামকরণ বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে , কোথাও লিখিতভাবে ককবরক এই নামটি নেই। ব্যাতিক্রম শুধু রাধামোহন ঠাকুরের ‘কক-বরক-মা’।
উল্লেখ্য, ত্রিপুরার ককবরক ভাষার উন্নতিকল্পে যে দুজন মনীষি অমর হয়ে আছেন তাঁরা হলেন ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ কর্তৃক ‘কাব্য বিনোদ’ উপাধিপ্রাপ্ত শ্রীচা দৌলত আহাহ্মদ এম এম দাহার এবং ‘সাহিত্য রতœ’ উপাধিপ্রাপ্ত শ্রীচা মাহাহ্মদ উমর। তাঁরা দুইজন যৌথভাবে রচনা করেরছিলেন ‘ককবরমা। অং ত্রিপুরা-ব্যাকরণ।’ নামক একটি গ্রন্থ। যা কুমিল্লার অমরযন্ত্র থেকে নীলাম্বর দত্ত চৌধুরী কর্তৃক পৌষ, ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দে মুদ্রিত হয় এবং পরবর্তিতে নিউ কুইক প্রিন্ট, ১১ জগন্নাথ বাড়ী রোড, আগরতলা থেকে ২২ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে পূনঃমূদ্রিত হয়। প্রকাশক হিসেবে ছিলেন পূর্ণ চন্দ্র দেববর্মা (হাচুকনি খরাঙ পাবলিশার্স, কৃষ্ণনগর, আগরতলা) । যদিও ‘ককবরমা। অং ত্রিপুরা-ব্যাকরণ।’ গ্রন্থটির প্রকাশকাল নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশকাল শ্রী রাধামোহন ঠাকুরের ‘কক-বরক-মা’ গ্রন্থ থেকে তিন বছর পূর্বে প্রকাশ হয়েছিল। আবার অনেকেই মনে করেন, এই দু’টো গ্রন্থই ১৯০০ সালের সমসাময়িক মাসগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং রাধামোহন ঠাকুরের গ্রন্থটি আগে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই শ্রী রাধামোহন ঠাকুরকে ককবরক ভাষার লিখিত রূপের পথিকৃত বলা হয়ে থাকে। তবে অনেক গবেষক ‘ককবরমা। অং ত্রিপুরা-ব্যাকরণ।’ গ্রন্থটির প্রকাশকাল হিসেবে ১৩০৭ ত্রিং এর পৌষ মাস হলে ইংরেজি ১৮৯৭সালে ডিসেম্বরের শেষে অথবা ১৮৯৮ সালের জানুয়ারির প্রথমদিকেই হবে বলে মত দিয়েছেন। তাঁদের অভিমত, যেহেতু পৌষ মাস ইংরেজি ডিসেম্বও ও জানুয়ারি মাসের অর্ধেক অর্ধেক সময় নিয়ে হয়। সুতরাং পৌষ মাসের প্রথম ভাগে হলে ১৮৯৭ খ্রি. আর শেষ ভাগের দিকে হলে ১৮৯৮ খ্রি. হবে। ড. দ্বিজেন্দ্র নারায়ন গোস্বামী পূণর্মদ্রিত গ্রন্থের ‘কিছু কথা’ লিখতে গিয়ে লেখেন-
“ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য। রাজ্যের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রাজ্যটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। প্রাচীন ঐতিহ্য প্রকাশের সংবাদে প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর মন গর্বে ভওে উঠে। ত্রিপুরী বা ককবরক ভাষা একটি প্রাচীন কথ্য ভাষা। নানা কারণে ভাষাটির নিজস্বলেখারূপ নেই। কিন্তু ভাষারূপে উহা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা। অনুজপ্রতিম শ্রীমান অরুণ দেববর্মা আমায় জানান যে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ত্রিপুরী ভাষাতে ব্যাকরণ লেখা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এই পুস্তক রাজ্যে পাওয়া যায়না। আমি খোঁজখবর শুরু করলাম । নানা প্রাচীন গ্রন্থাগাওে তল্লাসী চালিয়ে অবশেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একমাত্র কপি পেলাম শ্রী চা দৌলত আহম্মদ এর ‘ককবরমা’।
পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র ১৭ সেমি ী ১০.২ সেমি উহার আকার। অতি জরাজীর্ণ, হাত দিরেই পৃষ্ঠা ভেঙ্গে যায়। জেরক্সবা লেমিনেশান করতেদিওে কর্তৃপক্ষ নারাজ। বেশ কিছুদিন ধরে অতি সাবধানে শত পৃষ্ঠার পুস্ত নকল করেছি সাহিত্যপরিষদে বসে। পুস্তকখানি শ্রীচা দৌলত আহাহ্মদ এম এম দাহার এবং ‘সাহিত্য রতœ’ উপাধিপ্রাপ্ত শ্রীচা মাহাহ্মদ উমর এবং কুমিল্লা থেকে অমর যন্ত্রে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত নীলাম্বর দত্ত চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয় ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৭ খীষ্টাব্দের পৌষ মাসের প্রথমার্ধে হলেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ বহাল থাকবে।”
ককবরক ভাষার লিখিত রূপ আবিষ্কার যেন সমগ্র ককবরক ভাষাভাষী মানুষদের এ ভাষার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিল এই বাংলা ভাষাভাষী দুইজন মানুষ। আর এই সাল যদি সঠিক হয় তাহলে বোধহয় শ্রীচা দৌলত আহাহ্মদই ককবরক ভাষার লিখিত রূপের পথিকৃত, একথা বললে ভুল হবে না। এখন প্রশ্ন হল ‘ককবরক’ নামটি কে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন?
শ্রীচা দৌলত আহাহ্মদ এম এম দাহার তাঁর ‘ককবরমা। অং ত্রিপুরা-ব্যাকরণ।’ গ্রন্থের কেচেংছা বা ভূমিকা লিখতে গিয়ে ককবরক ভাষায় লিখেছিলেন-
“ওয়াঞ্জৈ কছল জাইতা তুইপ্রাছাব জাতি বুছুক তঙ্গো; আব জাতি কংচান দফা হিনো। যে আহাই, সিয়ো, কোয়াই তুইয়া, দুইসিং অং দেওসিং তেব বাসাল্ উমত্ব। উবর, কক্বাই, কক্ছাও ইমন ককবর হিনো।”
তিনি বাংলায় অনুবাদ করে লিখেছিলেন-
“সাধারণ বাঙ্গালী জাতির ন্যায় ত্রিপুরাগণও নানা শ্রেণিতে বিভক্ত; তাহাদের প্রত্যেককে দফা বলে। যথা সিয়ো, কোয়াই তুইয়া, দুইসিং বা দেওসিং বা বাসাল্ ইত্যাদি। ইহারা যে ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকে উহাই ত্রিপুরা ভাষা নামে আখ্যাত।”
শ্রীচা দৌলত আহাহ্মদ এম এম দাহার তাঁর ‘ককবরমা। অং ত্রিপুরা-ব্যাকরণ।’ গ্রন্থের ভূমিকায় ত্রিপুরাদের ভাষা হিসেবে ‘ককবর’ নামটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনিও পুরোপুরি ‘ককবরক’ শব্দটি লেখেননি। শেষের ‘ক’ টি বাদ দিয়ে ফেলেছেন অথবা তিনি ভাষার নামে এটি ব্যবহার করতে চাননি।
যাই হোক, ‘ককবরক’ শব্দটির উৎপত্তি বা লিখিতভাবে ব্যবহারের কথা যদি বলি তাহলে শ্রীচা দৌলত আহাহ্মদ এম এম দাহার তাঁর ‘ককবরমা। অং ত্রিপুরা-ব্যাকরণ।’ গ্রন্থে ১৩০৭ ত্রিপুরাব্দে ‘ককবর’ নামটি ব্যবহার করেন এবং ‘কক-বরক’ বা ‘ককবরক’ শব্দটি পুরোপুরিভাবে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৩১০ ত্রিপুরাব্দে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা তাঁর ‘কক-বরক-মা’ নামক গ্রন্থে। ’
[1]প্রভাষক, রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ, রাঙ্গামাটি।


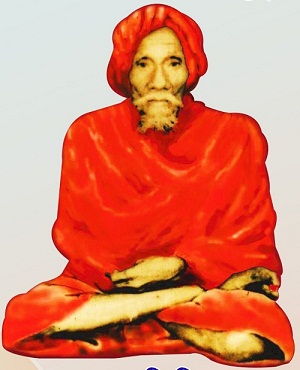

0 Comments