মুকুল কান্তি ত্রিপুরা
১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। যাদের আত্মত্যাগ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে এদেশের মানুষ তথা সারা বিশ্ব। প্রতিষ্ঠিত হবে সারা বিশ্বে শহীদ মিনার, পালিত হবে আন্তর্জিাতিক মাতৃভাষা দিবস, মর্যাদা পাবে সকল মাতৃভাষার ব্যবহারের সমান অধিকার।
আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে UNESCO ঘোষণা করে... “21 February is proclaimed
International Mother Language Day through the world to commemorate the myrters
who sacrificed their lives on this day in 1952." একটু দেরীতে হলেও জাতিসংঘ অর্থাৎ সারা বিশ্ব বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে,
মানব জীবনের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ভাষা আর সে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষ জীবনও উৎসর্গ করতে পারে। মায়ের ভাষায় কথা বলার আকুতি যে প্রাণের আকুতি তা বিশ্ববাসীর আর বুঝার বাকী রইলনা। যার তাড়না থেকেই আজকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাপ্তি। তার জন্য আমি গর্ব করি,
হ্যাঁ আমিও সে দেশেরই একজন সন্তান যে দেশের মানুষ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়ে্যিছল। আমি মনে প্রাণে কামনা করি বাংলা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা লাভ করুক।
দেশের বর্তমান সরকারকেও আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে স্বাধীণতার অনেক বছর পর হলেও বুঝতে সক্ষম হযেছে যে, এদেশে বাংলাভাষাভাষী মানুষ ছাড়াও অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষও রয়েছে। এদেশ বহু ভাষার দেশ। তারাও মায়ের ভাষায় কথা বলতে চায়, শিখতে চায়, পড়তে চায় এবং সর্বোপরি ঘরে-বাইরে প্রান খুলে কথা বলতে চায় নিজস্ব ভাষায়। যার তাড়না থেকেই হয়তোবা প্রাথমিক শিক্ষায় ক্ষুদ্র আকারে হলেও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রয়াস আমরা দেখেছি। এটি এ সরকারের একটি মহতি উদ্যোগ। যা সকল শ্রেণির মানুষ এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।
তবে ততক্ষণে
এদেশ থেকে যে কত ভাষা মুমূর্ষু সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে তার কোন বলার অপেক্ষা রাখেনা, যা আমি ককবরক ভাষাভাষী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে উপলব্ধি করতে
সক্ষম হয়েছি। কেননা বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একাংশ বর্তমানে
ককবরক ভাষায় কথা বলতে হিমসিম খাচ্ছে অথবা বলতে পারছেনা । তবে এরূপ পরিস্থিতির জন্য
কিন্তু তারা মোটেও দায়ী নয়। আমি মনে করি, তার জন্য দায়ী পারিপার্শিক বাধ্য পরিবেশ
ও রাষ্ট্র পরিচালনায় মাতৃভাষা সংরক্ষণ বা সমৃদ্ধির ব্যবস্থা না রাখা।
এখন আমার জীবনের
ঘটে যাওয়া একটি স্মৃতি খুব মনে পড়ছে...
আমি একদিন দুই তিনজন বাংলা ভাষাভাষী বন্ধুদের সাথে নিয়ে নিজ
ক্যাম্পাস জাহাঙ্গীরনগরের রাস্তায় হাটছিলাম। হঠাৎ বাড়ি থেকে ফোন আসলো। আমি কথা
বলছি মায়ের সাথে। আমার ককবরক ভাষায়। আর আমার বন্ধুরা বার বার আপত্তি করার চেষ্টা
করছে... যেন আমি বাংলায় কথা বলি। কারণ ওদের
যুক্তি হচ্ছে ওরা নাকি আমার ভাষা বুঝতে পারেনা । তাই ওদের সামনে
আমি যার সাথেই কথা বলি না কেন বাংলায় কথা বলতে হবে। তখন আমার একটু
খারাপ লাগলো। আমি বুঝানোর চেষ্টা করলাম এটি আমার ভাষা । এই ভাষাই আমি আমার মায়ের
সাথে কথা বলছি। তোমরা বললেও আমি আমার মায়ের সাথে অভিনয় করে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য
বাংলায় কথা বলতে পারবোনা। কিছুক্ষণ যুক্তিতর্কের হলো আর তখন থেকে তারা আর কখনো
আমাকে এভাবে বলেনা।
তবে এই উদাহরণটি
টানার অর্থ এই নয় যে আমি বাংলা বলতে পছন্দ
করি না। বরং বাংলার সঠিক উচ্চারণ শিখার জন্য আমি আবৃত্তি সংগঠনের কর্মশালাও ভর্তি
হয়ে কয়েক মাস উচ্চারণ শিখার চেষ্টা করেছি। ছোটকাল থেকে বাংলা মাধ্যমেই পড়ালেখা করে আসছি। বরং বাংলা
ভাষার প্রতি আমার আলাদা একটা টান আছে। কিন্ত তার মানে এই নয় যে, আমি আমার বন্ধুদের দেখানোর জন্য মায়ের সাথেও অভিনয় করে বাংলায় কথা বলবো।
বিশ্ববিদ্যালয়
জীবনে শিক্ষার্থী থাকাকালীন সময়ে চাঁদপুরের একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো
আমার। দেখা হলো জাতভাই সেখানকার
ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অনেকজনের সাথে। কথা হলে অনেক বিষয়ে। সমাজের বিভিন্ন ভাল-মন্দ বিষয় নিয়ে। ভাষার ক্ষেত্রে বোকার মতো একটি প্রশ্ন করেছিলাম....
“আপনারা অনেকেই বাংলায় কথা বলেন কেন?”
একজন বয়স্ক মহিলা উত্তরে জবাব দিলেন...
“আমরা ত্রিপুরা ভাষায় কথা বললে বাঙ্গালীরা
তিৎকারী মারে। অনেক খারাপ খারাপ কথা বলে।”
আমি রিতীমতো
অবাক হয়নি কারণ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার সাথে তিৎকারী না হলেও অন্তত বাধা এসেছিল
নিজ ভাষায় কথা বলতে।
ছোটকালে যখন
উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতাম তখন ত্রিপুরা আমরা হাতে গোনা ৫-১০ জন ছিলাম পুরো স্কুলে। আর বাকী সবাই চাকমা জনগোষ্ঠীর ছিল। তাই যখন ক্লাস
বিরতি হয় তখন আমরা ক্রিপুরা ভাষায় কথা বলতাম। তখন চাকমা বন্ধুরা বলে উঠতো...
“তোরা কি কথা বলিস? বুঝিনা সুঝিনা, চাকমা ভাষায় বল।”
তখন একটু মন খারাপ হলেও আবার চাকমা ভাষায় পারি
নাপারি কথা বলা শুরু করে দিতাম। কারণ তখনতো ছোট ছিলাম, একটু লাজ-লজ্জা,
ভয়-ভীতিও কাজ করতো। তাই একদম ক্লাস সিক্স এ এক বছরের মধ্যে চাকমা ভাষাটাকে যথাসম্ভব
রপ্ত করে ফেললাম।
এখানে অন্য
ভাষাভাষী মানুষকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার কোন ইচ্ছা বা প্রবনতা আমার নেই। কারো
যদি বিন্দুমাত্র খারাপ অনুভূতি আসে তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করে দিবেন। আমি শুধু
বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলছি। যা প্রতিটি পদে পদে মোকাবিলা করতে হচ্ছে বিভিন্ন
ভাষাভাষী মানুষের। তবে এরূপ পরিবেশ বা পরিস্থিতির জন্য কাকে দায়ী করবেন? একমাত্র নিয়তিকে দায়ী করা ছাড়া আর কোন
উপায় থাকেনা।
এখন ফিরে আসি
আবার আমার কতগুলো প্রশ্নের মধ্যে। প্রশ্নগুলো হলো,
১. যেসব অঞ্চলের ত্রিপুরাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠী যারা এরূপ
পরিস্থিতির শিকার তাদের জন্য
মাতৃভাষায় শিক্ষা দানে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?
২. যারা এখন নিজ মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেনা তাদের জন্য কোন
ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক
বা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে?
৩. তাদের জন্য কি মাতৃভাষা শিখানোটা আগে
জরুরী নাকি মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করাটা
আগে জরুরী?
৪. মাতৃভাষা না জানলে কিভাবে মাতৃভাষায়
শিখবে-পড়বে?
প্রশ্নগুলোর
উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকেই ভাবতে পারেন তাহলে কি মাতৃভাষায় শিক্ষা দান সম্ভব নয়? হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু একই
জনগোষ্ঠীর জন্য যদি একই শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয় তাহলে কেন ঐ জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ এই
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে ? কেনই বা তাদেরকে নিজস্ব ভাষা
প্রশিকক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারি-বেসরকারি বরাদ্ধ খাকবেনা? এটিই আমার প্রশ্ন। কারণ লক্ষ্যতো একটাই যে, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান করা।
ভাষা আন্দেলনের
বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি অতিক্রম করতে চললো। না পাকিস্তান সরকার এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছে
না বাংলাদেশ সরকার কথা বলেছে। জানিনা হয়তোবা আরেকটি একুশের অপেক্ষায় তারা ছিলো কিনা।
কিন্তু নিরবে নিবৃত্তে হারিয়ে গেছে এদেশ থেকে অনেক ভাষা এবং এখনো হুমকির সম্মুখিন বিভিন্ন
ভাষাগুলো। খুঁজলে ককবরক ভাষার মতো এরূপ পরিস্থিতির শিকার আরো অনেক ভাষাই পাওয়া যাবে হয়তোবা এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে।
সময় চলে যায় আর
কালের আবর্তে হারিয়ে যায় সেসব ভাষাগুলো। মানলাম ঐ ভাষাভাষী মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা
খুব বেশি পরিমাণে নেই। কিন্তু মায়ের ভাষা কে না বলতে চা্য়, কে না শিখতে চায় নিজের ভাষায়, কে না পড়তে চায় প্রাণের ভাষায়। কিন্তু
এখন সকল চাওয়ার মাঝেই অপূর্ণতা রয়ে গেছে শুধু দেশের সকল নাগরিকের এ ব্যপারে
সচেতনতা না থাকা এবং সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে । তবে সবাই সচেতন হলে, নিজ ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করলে এবং সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে এখান থেকে
মুক্তি পাওয়া তথা নিজ ভাষাকে
সমৃদ্ধ করা সম্ভব।


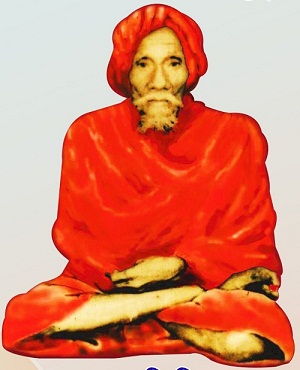

0 Comments